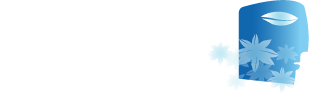অতি-চঞ্চলতা রোগটি এখন নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ মস্তিষ্কের বিকাশজনিত সমস্যায় এইসব লক্ষণ দেখা দেয়। এটি বৈজ্ঞানিক ভাবেও প্রমাণিত। এছাড়াও মস্তিষ্কে রাসায়নিক যেমন ডোপামিন, নরএপিনেফরিন প্রভৃতির হ্রাস-বৃদ্ধি ও এর কারণ হিসেবে কাজ করে। এই রোগের শক্ত বংশগত ভিত্তি রয়েছে। বংশগতি সূত্রে পাওয়া জিন ও পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় লক্ষণগুলো প্রকাশিত হতে থাকে। এগুলোর পাশাপাশি সুপ্রতিষ্ঠিত না হলেও মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব রয়েছে কিছু।
অনেকের মতে এখানে মূলত ইগোর সুসংগঠিত ও সমন্বিত উপায়ে কাজ করার ক্ষেত্রে সমস্যা থাকে। যদিও অতি চঞ্চলতার ক্ষেত্রে আচরণের সমস্যা থেকেই রোগ নির্ধারণ করার প্রবণতা বেশি দেখা যায় কিন্তু সেগুলো মনের অভ্যন্তরীণ সংঘাত বা দ্বন্দের সমস্যাকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করেনা। এখানে ইগোর কাজ করার পদ্ধতি গুলো বিভাজিত হয়ে পড়ে। ইগোর কাজ আরো অনেক বিষয় দিয়ে প্রভাবিত হতে পারে, যেমন মানসিক দ্বন্দ, পরিবেশের প্রভাব ইত্যাদি। এর ফলে ব্যক্তিত্বের সাম্যাবস্থা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ দেখা দেয়। মানসিক প্রক্রিয়া গুলো একে অপরের সাথে তাল মেলাতে পারেনা! নিজেকে নিজে পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা অনেক কম হয়। চিন্তার মধ্যে বিশৃঙ্খল কল্পনা, অস্বাভাবিক বিষণ্ণতাও চলে আসে সহজে।
পরিবেশ থেকে মনের ভিতর থেকে সবসময়ই উদ্দীপনার (তাড়না, অনুভূতি) জন্ম হয়। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। অতি চঞ্চলতা রোগের ক্ষেত্রে মন এইসব উদ্দীপনাকে নিয়ন্ত্রণ বা পরিমার্জন করতে পারেনা। ফলে এইসব উচ্চমাত্রার উদ্দীপনায় মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হতে থাকে। মূলত চার ধরনের সমস্যা উদ্ভুত হয়-১।মনোযোগ দেওয়া এবং রক্ষা করার প্রচেষ্টায় ঘাটতি ২। আবেগের বশে হটকারি কাজ করে ফেলা থেকে নিজেকে বিরত না রাখতে পারা ৩। পরিস্থিতির সাপেক্ষে তৈরি হওয়া উত্তেজনাকে প্রশমিত না করতে পারা ৪। অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ সমূহকে বাড়ানো বা রিইনফোর্সমেন্ট পাওয়ার প্রবণতা থাকা।
সমস্যা গুলো অনেক ছোটবেলা থেকেই বোঝা যেতে পারে। শিশুরা তাদের আচরণ, হাত পা নাড়াচাড়া ও আবেগকে সহজে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনা। আবার শান্ত হয়ে মনোযোগ ধরে রেখে ইতিবাচক মেজাজ বজায় রাখতে পারেনা। অনেক শিশুই অতিরিক্ত স্পর্শকাতর হয়। ফলে এরা কোন উদ্দীপনার মুখোমুখি হলে অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখায়! এটা হয়তো তাদের মনে কাজ করা অতিরিক্ত ভয় ও সতর্কতা থেকে আসে। আবার এটাও হতে পারে তাদের আচরণের প্রকৃতিটাই এমন থাকে যে নতুন অভিজ্ঞতার প্রতি নেতিবাচক মনোভাব দেখায়, সহজে গ্রহণ করতে পারেনা। এই সব ক্ষেত্রে শিশুর মনে বাইরের দুনিয়ার যে অভ্যন্তরীণ চিত্র (Internal Representation) তৈরি হয় তা অসম্পূর্ণ থাকে। ফলে বাস্তব জগতের অসংখ্য উদ্দীপনার ভিতরে পড়ে খুব সহজে চিত্তবিক্ষেপ বা মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে; অনেকে আবেগপ্রবণ হয়ে আচরণ করে। আবার কিছু শিশুর নতুন উদ্দীপনা পাওয়ার জন্য এতো বেশি আকাংখা থাকে যে তাদের নিজস্ব আচরণের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এই ধরনের শিশুরা ভীতিহীন ভাবে আগ্রাসী, হটকারি ও বিশৃঙ্খল আচরণ দেখাতে পারে। এবং এই রোগে কোন আচরণের ফলাফল ইতিবাচক বা নেতিবাচক যাই হোক না কেন সে সম্পর্কে উদাসীনতা থাকে। বিশেষ করে নিয়ম-কানুন মানার ক্ষেত্রেও আত্মনিয়ন্ত্রণ থাকেনা। সোজা কথায় আত্মনিয়ন্ত্রণ ও মস্তিষ্কের উচ্চতর কার্যনির্বাহী ক্ষমতায় (Higher executive functions) অনিয়ম হয় বা ঘাটতি দেখা দেয়। অতি চঞ্চলতায় অত্যধিক দুঃশ্চিন্তা প্রবণ হয়ে পড়ার প্রবণতা থাকে। এর ফলে অনেক সময় বাস্তবতা বোধ হারিয়ে কাজ করে তারা।
আন্তঃসম্পর্কের ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যপূর্ণ চিত্র পাওয়া যেতে পারে। যেসব ক্ষেত্রে পারস্পরিক যোগাযোগের প্রয়োজন কম সেসব ক্ষেত্রে সমস্যা না হলেও ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তৈরি খুবই কঠিন হয়। কারণ এই রকম সম্পর্কের জায়গায় সবসময় নতুন নতুন বিস্ময়ের সম্ভাবনা থাকে এবং সেখানে আত্ননিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার সুযোগ থাকেনা। এই রোগে পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার বোধ থাকায় এবং ব্যক্তিত্বে নারসিসিটিক ধরনের ভঙ্গুরতা থাকায় মানুষের সাথে আন্তঃসংযোগকে তাদের কাছে প্রচন্ড অগোছালো ও সমস্যার মনে হতে পারে। এই সমস্ত পরিস্থিতি একত্রে আরো নেতিবাচক ঘটনার জন্ম দেয়। একই ঘটনা শৈশবে পিতা-মাতা ও সন্তানের ভিতরের সম্পর্কেও ঘটে। অতি চঞ্চল শিশুদের মনে আইডেন্টিফিকেশন নামক ডিফেন্স মেকানিজম কাজ করায় তারা বাবা মার দেখানো আগ্রাসী মনোভাব নিজেদের মধ্যে ধারণ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে শৈশবকাল থেকেই কিছু বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে। মায়েরা এই শিশুদের সামলে রাখতে পারেনা সহজে। সম্পর্কের বন্ধনটা যেন অগোছালো মনে হয়! তার উপর এরা তাদের অন্য ভাই বোনদের সাথে অবিরাম মারামারি, সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে পারে। এর পিছনেও কিছু মানসিক বিষয় কাজ করে। এর মধ্যে ‘অবজেক্ট রিলেশন’ থিওরির ভূমিকা অন্যতম। এই তত্ত্ব ফ্রয়েডের তত্ত্ব থেকে কিছুটা আলাদা। এখানে বলা হয়েছে- মানুষ জন্মগত ভাবেই অন্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে। আর সম্পর্কের প্রকৃতি কেমন হবে তা নির্ভর করে ব্যক্তি সম্পর্কে শিশুর মনে কেমন প্রতচ্ছবি তৈরি হয় তার উপর ভিত্তি করে। তাদের মারামারিতে জড়িয়ে পড়ার বিষয়টি আসে অবজেক্ট রিলেশন ও আবেগ নিয়ন্ত্রণের সমস্যা থেকে সমন্বিত ভাবে। আবার যেহেতু এদের উদ্দীপনা নিয়ন্ত্রণে সমস্যা থাকে এরা দলবদ্ধ অবস্থায় কাজ করতে স্বস্তি পায়না। দল বা গ্রুপে একসাথে অনেক বেশি উদ্দীপনা আসে যা তাদের মানসিক ধারণ ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। তখন এরা এইরকম পরিস্থিতি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। এরকম পরিস্থিতি তাদের কাছে অসহনীয় লাগে।
একটা অদ্ভুত বিষয় হচ্ছে প্রায়শই এই শিশুরা ভিডিও গেম খেলা, ইন্টারনেট চালানো বা মুভি দেখা কোনরকম সমস্যা ছাড়াই করতে পারে। অমনোযোগিতা সেই সব বিষয়ে বেশি হয় যেসব তুলনামূলক কঠিন কাজ বা তাদের জন্য বিরক্তিকর। এবং যে কাজগুলো অন্যদের সাথে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপন করতে হয় সেগুলোতেও মনোযোগ দিতে পারেনা। ইমপালসিভিটি বা আবেগের বশে হটকারি কাজ করে ফেলার প্রবণতা হয়ত কাজ করে। বিশেষ করে কোন একটা কাজে নিজের পালা আসার জন্য অপেক্ষা করার জন্য যে মানসিক ক্ষমতা লাগে সেটা তাদের থাকেনা বা কম থাকে। সেখান থেকে তৈরি হয় অধিক দুঃশ্চিন্তা। আর যেহেতু আবেগ নিয়ন্ত্রণে এদের সমস্যা এমনিতেও থাকে তাই তারা গোছানো কাজ বা নিয়ম মেনে কাজ করতে সমর্থ হয়না বা কম পারে। তাদের অতি চঞ্চল আচরণ দুশ্চিন্তা কমানোর উপায় হিসেবে কাজ করে।
অনেকের মতে অতি চঞ্চলতা ও অমনোযোগিতা রোগে ম্যানিক ডিফেন্স কাজ করে। সিগ্মুন্ড ফ্রয়েডের মতে ব্যক্তি কোন একটা আকাঙ্ক্ষিত কিছুকে হারিয়ে ফেললে ম্যানিয়া তৈরি হয়! আকাঙ্ক্ষিত বিষয় বা অবজেক্ট হারিয়ে গেলে ইগো বিভক্ত হয়ে যায়। ইগোর একটা অংশ হারানো বস্ত বা ব্যক্তির সাথে আইডেন্টিফিকেশন করে বা সেটির রুপ ধারণ করার চেষ্টা করে। আরেকটি অংশ সেটির মুখোমুখি অবস্থা নেয়। অর্থাৎ অবজেক্ট যখন হারিয়ে যায় তখন এর প্রতি ব্যক্তির মনে একটি পরস্পর বিরোধী অনুভূতি বা এম্বিভেলেন্সের জন্ম হয়। যখন ইগোর একটা অংশ আরেকটা অংশকে আক্রমণ করে তখন আক্রান্ত অংশ নিজের উপর কাজ করা বিধি নিষেধ বা ইনহিবিশিনকে বাতিল করে দেয়। এর ফলে নিজেকে অভিনন্দিত বা বিজয়ী ভাবার মতো মুড তৈরি হয়! এই মুডে পৌছার জন্য চড়া দাম দিতে হয় ইগোকে। ইগো বাস্তবতার সাথে সম্পর্কহীন হয়ে পড়ে এবং বয়স অনুসারে বিকাশের নিম্নস্তরে নেমে যায়! ম্যালেনি ক্লিনের মতে ইগো বিভক্তির পাশাপাশি প্যারানয়েড সিজয়েড অবস্থা তৈরি হয়। ইগোর একটা অংশ অব্জেক্টকে ভালোবাসতে শুরু করে, আরেকটা অংশ ঘৃণা করতে শুরু করে। একসময় ইগোর কাছে মনে হয় যে সে হয়তো তার ভালো লাগা বা ভালোবাসার অবজেক্টকে ধ্বংস করে ফেলেছে। ম্যানিয়ায় গিয়ে ইগো এই খারাপ লাগাকে ভুলতে চেষ্টা করে। তারা মনে করতেন ম্যানিক ডিফেন্স থেকেই অমনোযোগিতা ও অতিচঞ্চলতার জন্ম!
ডা. সৌবর্ণ রায় বাঁধন
রেসিডেন্ট, ফেইজ-বি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়।
করোনায় স্বজনহারাদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য পেতে দেখুন: কথা বলো কথা বলি
করোনা বিষয়ে সর্বশেষ তথ্য ও নির্দেশনা পেতে দেখুন: করোনা ইনফো
মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক মনের খবর এর ভিডিও দেখুন: সুস্থ থাকুন মনে প্রাণে
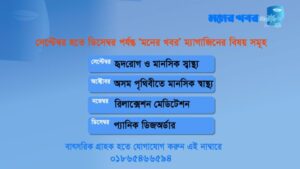
https://youtu.be/yTsoIJSddFA