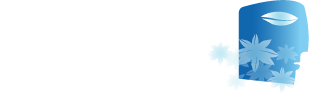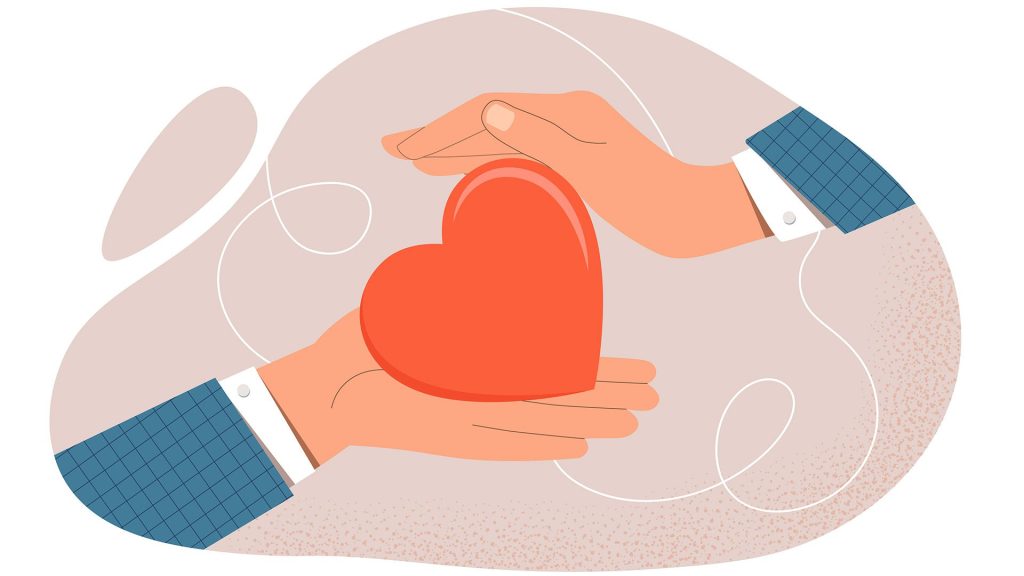ডা. সৃজনী আহমেদ
সহযোগী অধ্যাপক,
মনোরোগবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা কমিউনিটি মেডিক্যাল কলেজ
“আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসেনাই কেউ অবনী ‘পরে
সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে মোরা পরের তরে”
কামিনী রায়ের এই পদ্যটি পড়েনি বা শুনেনি অথবা এভাবে ভাবেনি— এমন মানুষ এই পাঠক সমাজে বিরল হবেন। পরার্থপরতার মূলভাবটি এখানে বেশ স্পষ্ট বলেই এই অবতারনা। এই যে ‘পরের কারনে স্বার্থ দিয়া বলি’ মনোভাবটি আসলে সমাজের জন্য কি উপকারী কিনা সেই প্রশ্নটাও পাঠকের মনে আসা স্বাভাবিক। পাঠকের কৌতুহলী মন জানতে চাইতেই পারে— পরার্থপরতায় সমাজ কি এগিয়ে যায়, নাকি একজনের স্বার্থের বলি করে জীবন,মন সকল উজাড় করাটা স্রেফ বোকামীর নিদর্শন!
মানব সমাজের ইতিহাসে প্রস্তর যুগে মানুষকে বাস করতে হতো দলবদ্ধ ভাবে। প্রকৃতির প্রতিকুলতা থেকে বাঁচতে যেমন গুহায় বাস করা লাগতো দলবদ্ধ ভাবে তেমন শিকার করার পর খাদ্য ভাগও হতো সবার মধ্যে। দলের প্রত্যেকের নিরাপত্তা অন্য সকল সদস্যের জন্যই দায়িত্ব থাকতো। ক্রমে ক্রমে প্রস্তর যুগের আধুনিক অবস্থা আসতে থাকলো, আরো বেশি শানিত হতে থাকলো অস্ত্র, আগুনের ব্যবহার —চাষাবাদ শুরু হতে থাকলো। প্রস্তর যুগ পার হয়ে ব্রোঞ্জ যুগের পর লোহার ব্যবহার শুরু হয়ে মানুষ গোত্রে গোত্রে ভাগ হয়ে চাষাবাদের সুব্যবস্থা, ধর্ম পালন, গবাদী পশু পালনের পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে সম্পর্কের ধারনাও গড়ে উঠতে থাকলো। নিজ গোত্রের একে অপরকে সাহায্য করা, চাষাবাদের জমি দখল বা শিকারের ভাগ নিয়ে যখন দ্বন্দ্বে জড়াতে হবে তখন নিজ গোত্রের সদস্যকে প্রাধান্য দেয়াই হলো নিয়ম। কিছু গবেষনা অনুযায়ী আজকের মানবজাতি বা হোমো স্যাপিয়েন্স টিকে থাকার কারন তাদের যুথবদ্ধ হওয়ার অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা। নিয়ান্ডারথাল অথবা হোমো ইরেকটাসরা স্যাপিয়েন্সদের সাথে এঁটে উঠতে পারেনি এই একতাবদ্ধতার কারনে। অর্থ্যাৎ হোমো স্যাপিয়েন্সদের এই ক্ষমতা তাদের অনন্য বৈশিষ্ট্য যে তারা নিজের স্বার্থ উপেক্ষা করে দলগত স্বার্থের জন্য জীবন বাজী রাখতে পারে। এই পরার্থপরতাই মানব সমাজের সুরক্ষা এবং অগ্রসরের একটি অনাবশ্যক উপাদান।
একটি সমাজের উন্নয়নে সমাজের একএক জন সদস্যের পরার্থপরতা তাদের নিজেদের আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলে, নিজেদের কে পূর্নতার একটি আশ্বাস দেয় এবং পারস্পরিক বন্ধন দৃঢ় করে৷
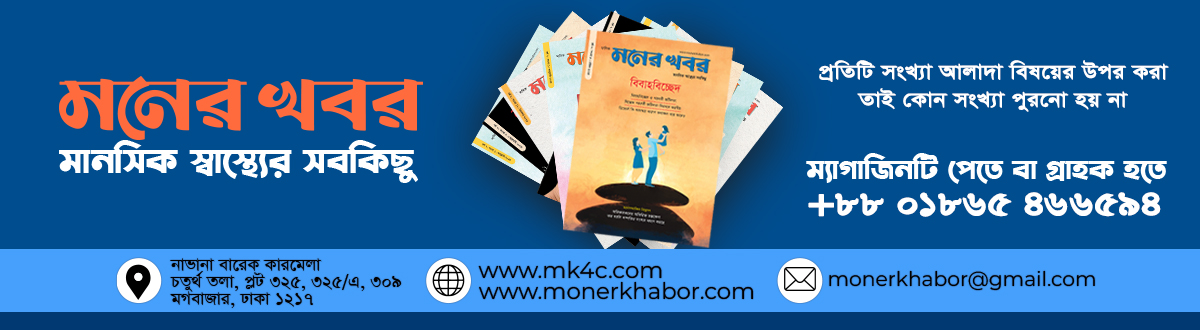
মানব সভ্যতার অগ্রসরমানতায় কৃষির পরে যখন আসলো দাস প্রথা, এবং সামন্ত প্রভুরা নিজেদের সম্পদ রক্ষার্থে বিভিন্ন নিয়মকানুনের বেড়াজাল তৈরী করলো। মানব জাতি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে বিভক্ত হয়ে গেলেও তাদের মধ্যে কোন না কোন ভাবে একতাবদ্ধতা প্রকাশিত হয়। এই বিষয়ে দ্বিমত আছে যে পরার্থপরতা একটি জিনগত বৈশিষ্ট্য নাকি পারস্পরিক আচরনের ভিত্তিতে পরার্থপরতার মনোভাব গড়ে উঠে। হ্যামিল্টন, ট্রাভিস প্রমুখ গবেষকের মতে পরার্থপরতা জিনগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দেখা যায়। আবার আরেকদল গবেষকের মতে পরার্থপরতা একজনকে দেখে আরেকজনে অভ্যাস হিসেবে আসে৷ এই বিষয়ে বিস্তারিত অন্য লেখায় পাঠক জানতে পারবেন। এই লেখার যেটা উদ্দেশ্য সেই প্রসংগে বলার যে — যেকোন ভাবেই হোক পরার্থপরতা সমাজকে গতি দেয়। যেমন— সমাজে একটা প্রাকৃতিক বা মানবিক দুর্যোগে দেখা যায় বিপন্ন মানুষকে উদ্ধারে এগিয়ে আসেন অনেকে। সেখানে দল—মত— ধর্ম—বর্ন নির্বিশেষে মানুষ এগিয়ে আসে অন্য কে সাহায্য করতে— এমন কি নিজের বিপদ— অসুবিধা তুচ্ছ করে। আবার সমাজে অর্থ দানের মাধ্যমে তৈরী হয় অনেক দাতব্য প্রতিষ্ঠান— যেই প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবায় গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখে। একই সাথে পরার্থপরতা সমাজে সকলের অংশগ্রহনে উতসাহ দেয়৷ একে অপরকে সাহায্য করলে ভালো অনুভুতি ছড়িয়ে পড়ে, যা সমাজের উন্নত বৈশিষ্ট্য যেমন পারস্পরিক বন্ধুত্ব, সহমর্মিতার চর্চার সংস্কৃতি গড়ে উঠে। এতে করে সমাজে গতিশীলতা আসে, উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্ভব হয়।
স্বার্থপরতা সমাজের এক একজন মানুষকে বানিয়ে ফেলে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত, এমনকি তখন ব্যক্তিগত ভোগবাদীতা তাকে এক অর্থে হতাশ করে ফেলে৷ কিন্তু যখনই ভোগবাদীতা ছুঁড়ে ফেলে কেউ দান করা, উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহন করায় যোগদান করে, তখন একটি বৃহত্তর স্বার্থের অংশ হওয়ায় একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তিরও নিজেকে বৃহত্তর স্বার্থের অংশ হিসেবে নিজেকে অপেক্ষাকৃত সুখী অনুভব হয়। এভাবে পরার্থপরতা সামষ্টিক অনুভবকে গড়ে তুলে।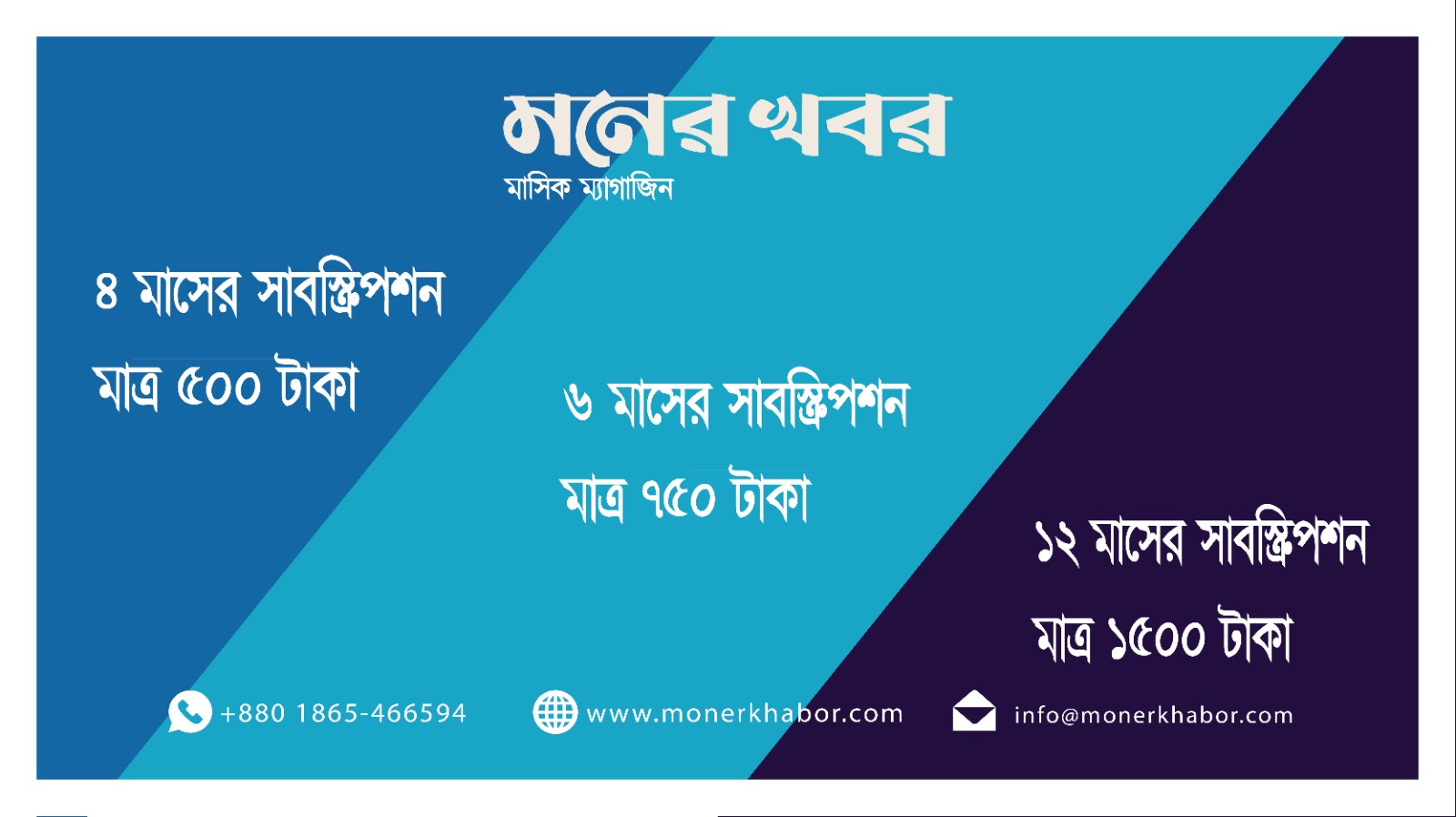
সামাজিক উন্নয়নে পরার্থপরতার খুব সহজ উদাহরন হচ্ছে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো৷ পৃথিবী যখন জলাতংক রোগের আতংকে তখন একজন বিজ্ঞানী নিজের জীবন বিপন্ন করে হলেও সেটার টিকা তৈরীতে উঠে পড়ে লাগলেন। লুই পাস্তুর যখন নিজের শরীরের উপরই পরীক্ষা করতে যাবেন তখন একজন মা তার আক্রান্ত সন্তানকে নিয়ে আসলেন বলে গোটা বিশ্ব এই আবিষ্কারের সাক্ষী হলো। এখনও দলগতভাবে বিজ্ঞানীরা লড়াই করেন এরকম একটা প্রতিষেধক, একটা জীবন বাঁচানোর প্রক্রিয়ার জন্য। এই ক্ষেত্রে নিজ স্বার্থ গৌন হয়ে যায়, এবং সেই প্রক্রিয়াতেই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়। বিশ্ব যখন কভিড ১৯ এর অতিমারীর সাক্ষী হলো তখনও এর প্রমান দেখলো৷ ভুটান, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া রাষ্ট্রীয় ভাবে নিজের দেশের সংকটগুলো মোকাবিলা করলো, পক্ষান্তরে অতটা পেরে উঠলোনা স্বার্থবাদী রাষ্ট্রগুলো। মৃত্যু কম বেশি যাই হোক,অর্থনৈতিক— সামাজিক সংকট নিয়ে অনেক দেশ আজও ধুঁকছে।
তাই পরার্থপরতা থেকে আসা সহনশীলতা, সহমর্মিতা, সামগ্রিকতা, সামষ্টিকতা— এই উপাদানগুলোই সমাজের সুরক্ষা আর উন্নতির সহায়ক৷ তাই পরার্থপরতার সংস্কৃতি সমাজের উন্নয়নের অন্যতম নিয়ামক।
এই বোধের সঞ্চারন হোক সকলের মাঝে আর উন্নয়ন আসুক পৃথিবীতে ।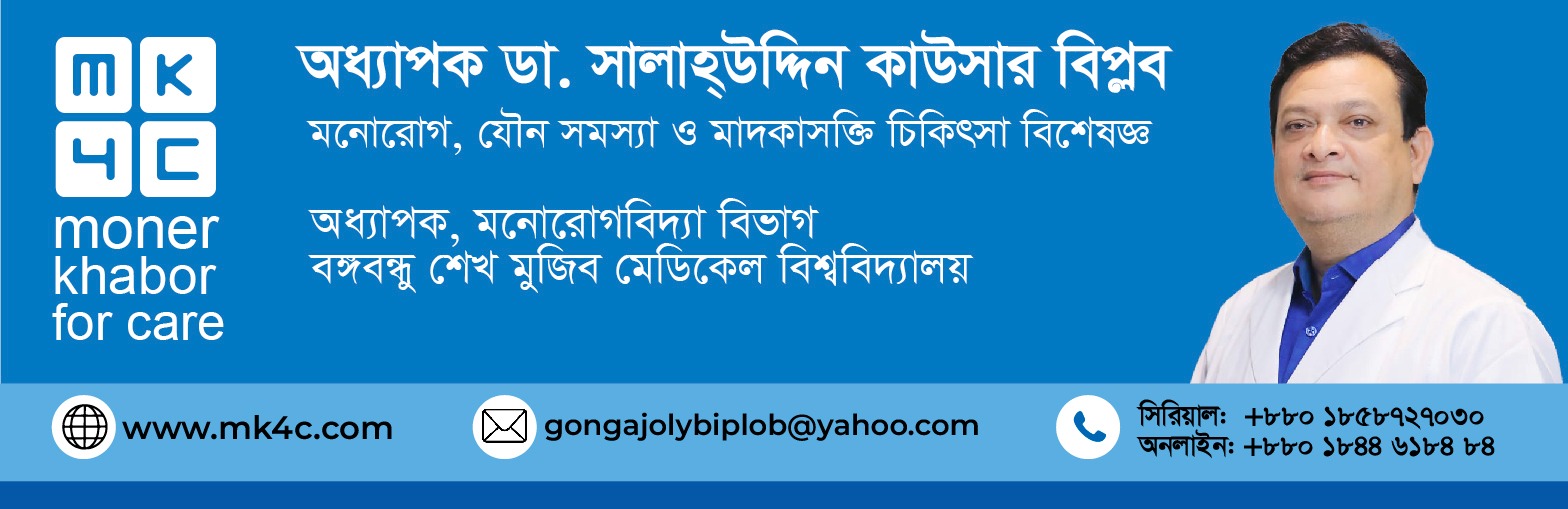
এপোয়েন্টমেটের জন্য এখানে ক্লিক করুন- Prof. Dr. Shalahuddin Qusar Biplob
আরও দেখুন-