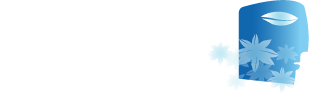এক সময় মানসিক রোগের নাম শুনলেই মানুষ সরে যেত দূরে, চিকিৎসা নিতে লজ্জা পেত কিংবা সামাজিক কুসংস্কারের ভয়ে চুপ করে থাকত। আজও সেই সংকোচ পুরোপুরি দূর হয়নি, তবে ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে পরিস্থিতি। মানসিক স্বাস্থ্যকে ঘিরে বাড়ছে সচেতনতা, বাড়ছে চিকিৎসাসেবার চাহিদা। এ বাস্তবতায় মানসিক স্বাস্থ্যসেবার বর্তমান অবস্থা, এর চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা নিয়ে আমরা কথা বলেছি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল’র মানরোগবিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহযোগী অধ্যাপক ডা. পঞ্চানন আচার্য্য‘র সঙ্গে।
মনের খবর: কেমন আছেন?
শুরুতেই ধন্যবাদ, আমাকে আপনাদের আয়োজনে যুক্ত করার জন্য। আছি, স্বাভাবিক নিয়মেই ভালো আছি।
মনের খবর: সাম্প্রতিক সময়টা কেমন কাটছে আপনার?
ডা. পঞ্চানন আচার্য্য: ‘খারাপ না’- এই অর্থে ভালোই কাটছে। এমনিতে অনেক ব্যস্ততার ভিতরে আছি, সেটা অবশ্যই ভালো দিক। আমি মনে করি ব্যস্ত থাকা মানে হচ্ছে এই জগৎ-সংসার এখনও কিছু আশা করছে আমার কাছ থেকে- এটা আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। আমি নিরিবিলি, আপনমনে কাজ করে যেতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি, জগতের কাছে আমার খুব বেশি দাবী নেই, আসলে দাবী করতেও পারি না। তাই, কাজ করাটাই আমার নিজের কাছে নিজেকে প্রমাণের একমাত্র অবলম্বন। সেই অর্থে ভালো যাচ্ছে সময়টা। আবার, প্রচণ্ড ব্যস্ততার মাঝে, কাজের ভীড়ে নিজের কাছে নিজেকে হারিয়ে ফেলার অনুভূতি হয় যখন, মনে হয় যে নিজের সাথে নিজে একটু থাকতে পারছি না, নতুন কিছু ভাবতে পারছি না, নতুন কিছু লিখতে পারছি না, তখন অনেক খারাপ লাগে। সব মিলিয়ে সময়টা অনেক উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে।
মনের খবর: মানসিক রোগ চিকিৎসার পেশায় আপনার আগ্রহ কীভাবে তৈরি হয়?
ডা. পঞ্চানন আচার্য্য: ছোটবেলা থেকেই প্রচুর বই পড়তাম, যার অধিকাংশই উপন্যাস, বিভিন্ন ধরণের; যেখানে মানব মনের গতিপ্রকৃতি খুব টানতো। এছাড়াও হিন্দু ধর্মীয়, সুফিবাদ, আবার মিসির আলি ধরণের সাহিত্যও পড়তাম- সব কিছু মিলেই আমার মনে মানুষের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে প্রচন্ড আগ্রহের জন্ম দেয়। এর মধ্যে যখন সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেলে তৃতীয় বর্ষে উঠলাম, সাইকিয়াট্রিতে লেকচার দিতে আসলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ডা. গোপাল শংকর দে স্যার। স্যারের একেকটা লেকচার ছিল যেন সাহিত্যের ক্লাস, তার মধ্যে সাইকিয়াট্রি আলোচনা। আর উনার ব্যক্তিত্বের জাদু ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। যারা শুনেছেন তারাই শুধু বুঝতে পারবেন কি মোহময় করে ফেলতেন তিনি তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের। তখনই স্থির করি যে, সাইকিয়াট্রি পড়বো। এমনভাবেই ভাবতাম, আমার সহপাঠীরাও একেবারে নিশ্চিত ছিল যে আমি সাইকিয়াট্রিস্ট হবো। মজার বিষয় হচ্ছে, আমি তখন এটাও জানতাম না যে, সাইকিয়াট্রি আর সাইকোলজি দুটো আলাদা বিষয়।
মনের খবর: দীর্ঘ অভিজ্ঞতার এই পথে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ও প্রাপ্তি কোনটি বলে মনে করেন?
ডা. পঞ্চানন আচার্য্য: অভিজ্ঞতা দীর্ঘ কিনা একমত নই, তবে এর মধ্যে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো- সাইকিয়াট্রি, মানসিক রোগ, মানসিক চিকিৎসার সব কিছু নিয়ে তীব্র নেতিবাচক মনোভাব। জনগণের মধ্যে তো অবশ্যই, দুর্ভাগ্যের বিষয়, অন্য বিষয়ের অনেক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মধ্যেও এই মনোভাব বর্তমান। আমার কাছে এটাই বড় চ্যালেঞ্জ মনে হয়। আর প্রাপ্তি বলতে- যারা সুস্থ হয়ে উঠেন তাঁদের কাছ থেকে যখন তাঁদের স্বস্তির কথা শুনি, তাঁরা যখন অন্য কাউকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মানসিক রোগের চিকিৎসা নিতে পাঠান, সেটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। আমার মনে হয়, এটা শুধু আমার নয়, আমাদের সকল সাইকিয়াট্রিস্টেরই এরকম অভিজ্ঞতা হয়, এই প্রাপ্তিটা হয়। এছাড়া আমার আর কিছু প্রাপ্তি বলতে আমি মনে করি- আমার স্বল্প সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে আমার কিছু ছাত্র-ছাত্রীকে সাইকিয়াট্রির প্রতি আগ্রহী করে তুলতে পেরেছি, তাদের সাথে আমি কিছু গবেষণা কাজ চালাতে পেরেছি- সাইকিয়াট্রির একজন শিক্ষক হিসেবে এটাও একটা বড় প্রাপ্তি।
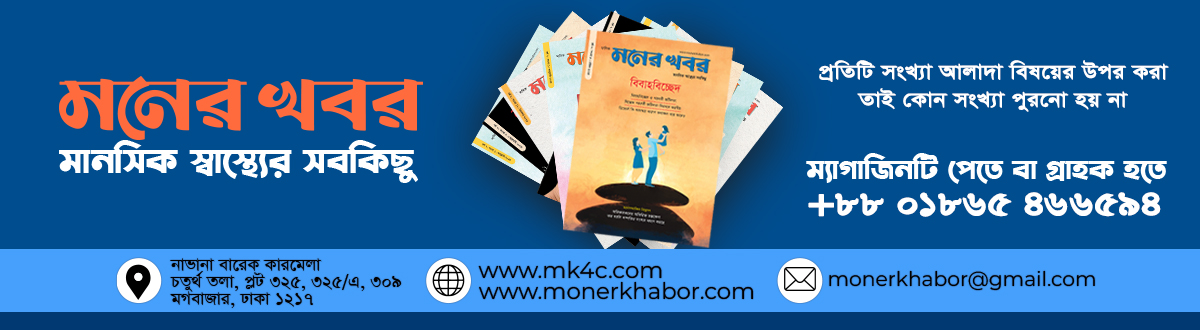
মনের খবর: বর্তমানে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মানসিক রোগ বিভাগের সেবা কাঠামো ও চিকিৎসার ধরন সম্পর্কে একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরবেন কি?
ডা. পঞ্চানন আচার্য্য: বাংলাদেশের স্বাস্থ্যচিকিৎসা প্রদানের কাঠামোটা যথেষ্ট জটিল। তাই, কারো কারো বুঝতে একটু অসুবিধা হতে পারে। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মনোরোগবিদ্যা বিভাগ প্রধানত তিন ধরণের কার্যক্রম পরিচালনা করে।
প্রথমতঃ চিকিৎসা প্রদান। এখানে বহির্বিভাগে প্রতিদিন শতাধিক লোক চিকিৎসা নেন। এখানে সরকারী ভাবে ২৩ শয্যার অতিরিক্ত শয্যা মিলিয়ে মোট ৬০ শয্যার অন্তর্বিভাগ রয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশে মানসিক রোগীদের জন্য শুধু ২ টি হাসপাতাল- জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল এবং মানসিক হাসপাতাল, পাবনা; ছাড়া আর কোথাও এত শয্যার অন্তর্বিভাগ নেই। এখানে রয়েছে সপ্তাহের ছয় কর্মদিবসে অর্থাৎ শনি থেকে বৃহস্পতিবারে ছয়টি বিশেষায়িত ক্লিনিক, যেখানে ১০ টাকার সরকারী বহির্বিভাগের টিকেট কিনে যে কেউ সকাল ১১ টা থেকে ১ টা পর্যন্ত সমস্যাভিত্তিক বিশেষায়িত চিকিৎসা পেতে পারেন। প্রসঙ্গতঃ জানিয়ে রাখছি- শনিবারে রিলাক্সেশন এবং প্যারেন্টিং ক্লিনিক, রবিবারে সাইকিয়াট্রিক সেক্স ক্লিনিক, সোমবারে এডিকশন প্রিভেনশন ক্লিনিক, মঙ্গলবারে শিশু-কিশোর মানসিক রোগ ক্লিনিক, বুধবারে ওসিডি ক্লিনিক, এবং বৃহস্পতিবারে ডিপ্রেশন ক্লিনিক।
দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা কার্যক্রম। এখানে নিয়মিত এমবিবিএস, ডেন্টাল, নার্সিং এর স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম, ট্রেনিং প্রদান করা হয়। একই সাথে এখানে সরাসরি এফসিপিএস (সাইকিয়াট্রি)-র প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এছাড়াও অন্যান্য বিভাগের স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণার্থীদেরও সাইকিয়াট্রির প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
তৃতীয়তঃ গবেষণা কার্যক্রম। এখানে বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন দেশি-বিদেশি গবেষক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে গবেষণা কার্যক্রম চলমান আছে। যার মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে।
মনের খবর: মানসিক রোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মানুষের মধ্য সচেতনতা ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি কতটা বদলেছে বলে আপনি মনে করেন?
ডা. পঞ্চানন আচার্য্য: আমার মনে হয়, সচেতনতা বেড়েছে, আর তাই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী কমেছে। আমাদের স্যার বা ম্যাডামদের কাছ থেকে যখন এ দেশে মানসিক রোগ নিয়ে শুরুর দিকে ধারণাগুলো শুনতে পাই, তখন তো মনে হয় আমরা অনেক ভালো অবস্থান থেকেই শুরু করেছি। তবে, এটাও ঠিক যে, এখনো অনেক নেতিবাচকতা রয়ে গেছে- মানসিক রোগ নিয়ে, রোগের চিকিৎসা নিয়ে, বিশেষতঃ ঔষধ নিয়ে। যে সব বিষয় এখনো মানসিক চিকিৎসার অন্তরায়।
মনের খবর: চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মানসিক রোগ বিভাগে কী কী ধরণের মানসিক রোগের চিকিৎসা দেওয়া হয়?
ডা. পঞ্চানন আচার্য্য: এ বিষয়ে আগেই বলেছি কি কি চিকিৎসা দেয়া হয়ে থাকে এখানে। তবে, এক কথায় সব ধরণের মানসিক রোগের চিকিৎসা দেয়া হয়।
মনের খবর: বর্তমানে কোন কোন আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি বা থেরাপি বর্তমানে চালু রয়েছে?
ডা. পঞ্চানন আচার্য্য: এখানে বিশেষায়িত ভাবে কাউন্সেলিং করা হয়, ইলেক্ট্রোকনভালসিভ থেরাপি চালু আছে, যেটার সুযোগ বাংলাদেশের সকল মেডিকেল কলেজের মধ্যে একমাত্র এখানেই আছে।
মনের খবর: সরকারি পর্যায়ে মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় আপনার দেখা সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা কোনটি?
ডা. পঞ্চানন আচার্য্য: প্রথমেই বলবো, তীব্র জনবল সংকটের কথা। ৬০ শয্যার ওয়ার্ড হলেও, আমার এখানে ওয়ার্ড বয়ের সংখ্যা এমনই যে, মাঝে মাঝে তিনবেলা একজন করে ডিউটি দেয়াও সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে, ভর্তি রোগীদের ব্যবস্থাপনা অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ আর্থিক সীমাবদ্ধতা। এই যে এত বড়ো একটা মনোরোগবিদ্যা বিভাগ তার বিশাল কর্মযজ্ঞ নিয়ে চলছে, এর জন্য আলাদা কোন বরাদ্দ আসলে নেই।
মনের খবর: যখন সরকারি প্রক্রিয়ায় কোনো কাজ সম্পন্ন করতে দীর্ঘ সময় লাগে, তখন কি ব্যবস্থা গ্রহন করেন?
ডা. পঞ্চানন আচার্য্য: অন্য দশটা ওয়ার্ডের মতোই এখানে রোগীদের বিভিন্ন বিষয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকার থেকে আসে, যা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। আর একটা সরকারী দপ্তর চালাতে হলে এর বাইরেও যেসব আলাদা কিছু বরাদ্দ লাগে, ধরুন দাপ্তরিক কাগজপত্র, একটা আলাদা অফিস কক্ষ, অফিস সহায়ক এসবের কোন কিছুই নেই। এখানে একটি সরকারী চিঠি লিখতে হলে তা আমাকেই টাইপ করতে হয়, আমাকেই নিজ উদ্যোগে প্রিন্টার ও অফসেট কাগজের ব্যবস্থা করতে হয়। এর জন্য আলাদা কোন বরাদ্দ নেই। আর আছে দাপ্তরিক দীর্ঘসূত্রিতা। ধরা যাক, আমার একটা দরজা ভেঙ্গে গেলো, জানালার কাচ ভেঙ্গে গেলো, বা রোগীদের শৌচালয়ে কোন একটা সমস্যা হলো। এখন সেটা ঠিক করতে হলে পরিচালকের মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগকে জানাতে হবে, সেই চিঠি তাঁরা কোন একদিন দেখবেন, তারপর এই বছরের বাজেটে আর অর্থ বরাদ্দ নেই, তাই পরের বছরের জুলাই মাসের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, অথবা লোক পাঠিয়ে ঠিক করবে করবে বলে আর লোক না পাঠানো।
মনের খবর: অনেকগুলো তাগাদার মধ্যে অল্প কিছু কাজ করে বাকিগুলো বিভিন্ন কারণেই আর করা হলো না। তখন কি করেন?
ডা. পঞ্চানন আচার্য্য: সরকারী ভাবে করতে গেলে এই সামান্য কাজটার জন্য কখনো কখনো এক বছরও অপেক্ষা করে নাও হতে পারে। একটা অনিশ্চয়তা। কিন্তু আপনি তো এভাবে বসে থাকতে পারবেন না, নিরাপত্তা সহ বিভিন্ন বিষয় জড়িত। তখন কি হয়? আমরা নিজের পকেটের টাকা দিয়ে টুকটাক এটা সেটা সারিয়ে নেই, চালিয়ে যাই, এভাবেই চলে।
মনের খবর: নিজ খরচে এইসব কাজ করেও লাভের জায়গা কোথায় দেখেন আপনি?
ডা. পঞ্চানন আচার্য্য: লাভ হচ্ছে- আরো দশটা যন্ত্রণা ভোগ করা থেকে বাঁচি, কোন একটা ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকি, কাজগুলো শেষ হয়। অন্যথায়, কোন একটা অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে গেলে দায়-দায়িত্ব বা জবাবদিহি তো আমাকে ঠিকই করতে হবে। বলতে পারেন, ঝামেলা থেকে বাঁচতে এভাবেই চালিয়ে যাই, বা চালিয়ে যেতে হয়। এগুলোই সীমাবদ্ধতা।
মনের খবর: মানসিক রোগ নিয়ে সমাজে প্রচলিত ভুল ধারণা ও কুসংস্কার কীভাবে চিকিৎসা গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করছে?
ডা. পঞ্চানন আচার্য্য: চিকিৎসা গ্রহণে বাধা সৃষ্টির বিষয়টি বহুমাত্রিক। যেমন- অনেকেই মনে করেন মানসিক রোগ বলতে কিছুই নেই। কারো কাছে জ্বীনভূতের বিষয়, কারো কাছে মনের জোর না খাটানোর কারণে, আবার কারো কাছে ইচ্ছাকৃত ঢং। অন্যদিকে অনেকেই, এমনকি চিকিৎসকদের মধ্যেও- সাইকোলজিস্টদের মধ্যেও, মনে করেন মানসিক রোগে শুধু কাউন্সেলিং করাই যথেষ্ট। ঔষধ খাওয়ার কোন দরকার নেই, ঔষধগুলো ক্ষতিকর, এরকম আরো অনেক কিছু। ফলে, রোগীরা চিকিৎসার আওতায় আসেন না, চিকিৎসা শুরু করে মাঝপথে বন্ধ করে দেন।
মনের খবর: আপনি কীভাবে মানসিক রোগ চিকিৎসার এই সামাজিক বাধাগুলো ভাঙতে কাজ করছেন?
ডা. পঞ্চানন আচার্য্য: আমি ব্যক্তিগতভাবে যখন যেখানে সুযোগ পাই, এই বিষয়গুলো নিয়ে সরাসরি কথা বলি। বিভিন্ন সভায়, সেমিনারে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের কাছে এই কথাগুলো তুলে ধরি, লেখালেখি করি, টিভিতে আলোচনা করি।
মনের খবর: বিভাগীয় প্রধান হিসেবে আপনার তত্ত্বাবধানে ইতোমধ্যে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগগুলো সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?
ডা. পঞ্চানন আচার্য্য: আমি বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব নেয়ার আগ থেকেই ২০১৯ খ্রিঃ এর সেপ্টেম্বরে নিজ উদ্যোগে চালু করি ‘স্টুডেন্টস কাউন্সেলিং সেন্টার’- যেটা বাংলাদেশের সকল মেডিকেল কলেজের মধ্যে প্রথম উদ্যোগ। বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব নিই ২০২০ খ্রিঃ এর শুরুতে। তখন এই বিভাগে আমি একাই ছিলাম- সাথে শুধু একজন সহকারী রেজিস্ট্রার। শুরুতেই আমি নিজের খরচে, প্রায় অর্ধলক্ষ টাকার বেশি; ওয়ার্ডে অবকাঠামোগত সংস্কার করে এটিকে একটা সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ওয়ার্ডে রূপান্তর করার চেষ্টা করি, যেকোন জায়গায় অবস্থান করেও সার্বক্ষনিক তদারকির জন্য সিসি ক্যামেরা স্থাপন করি। একই সাথে এই বিভাগের চিকিৎসা কার্যক্রমকে দুইটি মূলনীতির উপরে পরিচালনা করা শুরু করি- একটি Evidence Based Practice, আরেকটি Bio-psycho-social Approach. ফলে, প্রেস্ক্রিপশনে ঔষধের সংখ্যা কমা সহ বিভিন্ন ভাবে চিকিৎসার মান উন্নত হয়। আর ঔষধের পাশাপাশি কাউন্সেলিং বা সাইকোথেরাপির বিষয়টিও চালু করি। এর সাথে সাথে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজি বিভাগের সাথে কিছু আলাপ হয়- কাউন্সেলিং বিষয়ে যৌথ উদ্যোগ নেয়ার জন্য, অন্যদিকে CRP, চট্টগ্রাম-এর সাথে একটা যৌথ প্রটোকল তৈরিতে হাত দেই- যাতে করে এখানে চিকিৎসা নেয়া মানসিক রোগিদের জন্য আলাদা প্রশিক্ষণ বা রিহ্যাবিলিটেশনের সুযোগ তৈরি হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ঠিক এই সময়টাতে কোভিড পর্ব শুরু হওয়াতে আমার সব উদ্যোগ মুখ থুবড়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত সেই স্থান থেকে পুরো ওয়ার্ডটাই উপরের তলায় স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। স্থানান্তরের এই পর্বটা ছিল যথেষ্ট সংগ্রামের- যার বিস্তারিত এখানে বলতে চাইছি না। পরবর্তীতে আমি বিভাগের ফাইলপত্র, অফিসিয়াল প্যাড, রেফারেল কাগজ, ডকুমেন্টেশন পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ পরিবর্তন আনি- যেটা আসলে এই বিভাগের কার্যক্রমকে একটা গ্রহণযোগ্য বা সম্মানজনক অবস্থানে নিয়ে গিয়েছে বলে আমি মনে করি। এই সময়ে আমার সাথে সহকর্মী ডা. হিমাদ্রি মহাজনও যোগ দেন। একটা লোগো তৈরী করি যেখানে আমাদের বিভাগের মূলনীতি স্থির করি- Mind- We Care. আমরা তিনজনে মিলে সবকিছুকে একটা নিয়মের মধ্যে আনার চেষ্টা করি এবং বিভিন্নভাবে সৌন্দর্যবর্ধন করি। আমি দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে এখানে পুর্নোদ্যমে এফসিপিএস (সাইকিয়াট্রি) প্রশিক্ষণ শুরু হয়, আমি এই প্রশিক্ষনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট শিডিউল তৈরি করেছি। আমার মতে এতে করে প্রশিক্ষণের মান অনেক উন্নত হয়েছে। এরপর আমি সহকর্মীদের সহায়তায় একে একে ছয়টি বিশেষায়িত ক্লিনিক চালু করেছি- যা বিস্তারিত আগেই বলেছি।
মনের খবর: একাডেমিক কার্যক্রমে অন্যান্য বিভাগের সাথে সমন্বয়ের অভিজ্ঞতা কেমন?
ডা. পঞ্চানন আচার্য্য: আমি একাডেমিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এই মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন বিভাগকে সাথে নিয়ে নিয়মিত অনেক সফল সেমিনার আয়োজন করেছি, যা এই বিভাগের জন্য গৌরবের। এছাড়া, স্নাতক পর্যায়ের ছাত্র-সহ বিভিন্ন পর্যায়ের গবেষকদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে মনোরোগবিদ্যা বিভাগকে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি গবেষনার সাথে যুক্ত করেছি। এক পর্যায়ে এই বছরের শুরুতে চালু করেছি ‘সাইকিয়াট্রিক রিসার্চ সেল’- যার মাধ্যমে এই বিভাগের গবেষণা কার্যক্রম আরো কাঠামোবদ্ধ ও গতিশীল হয়েছে।
মনের খবর: সম্প্রতি শুরু হওয়া মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিহেভিয়ার থেরাপিস্টের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম থেকে কী ধরনের বাস্তব সুবিধা পাবেন বলে আশা করছেন?
ডা. পঞ্চানন আচার্য্য: আমরা মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিহেভিয়ার থেরাপিস্টের মাধ্যমে এখানে একটা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করেছি- যেখানে এই বিভাগের প্রশিক্ষণার্থী ও চিকিৎসক-সহ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থীরাও প্রশিক্ষণ পাবেন। এর মাধ্যমে আমরা আমাদের ওয়ার্ডে চিকিৎসা নিতে আসা বাচ্চাদের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আরো আধুনিক ABA Therapy দিয়ে উপকৃত করতে পারবো বলে মনে করি।
মনের খবর: ভবিষ্যতে বিভাগটির উন্নয়নের জন্য আপনি কী ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চান?
ডা. পঞ্চানন আচার্য্য: পরিকল্পনা তো আসলে অনেক। কিন্তু আমরা সবাই এতো কাজের চাপে থাকি- তাই অনেক কিছুই সময় ও সুযোগের অভাবে করা হয়ে উঠে না। যেমন- আমাদের দুইটা প্রকল্প চালুর অপেক্ষায় আছে অনেকদিন। একটিতে সকল বিভাগের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের প্রশিক্ষনার্থিদেরকে সাইকিয়াট্রি বিষয়ে একটা বেসিক কোর্স-এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। আরেকটি আমরা পর্যায়ক্রমে অন্য বিভাগের সাথে, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সাথে সমন্বয় করে ওদের ওখানেই সাইকিয়াট্রিকে নিয়ে যাবো- যাতে সাইকিয়াট্রির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সবার মধ্যে জানার পরিধি বাড়ে।
মনের খবর: মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা প্রসারে কি ধরনের উদ্যাগ নিয়েছেন?
ডা. পঞ্চানন আচার্য্য: মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা দেয়ার পরিধি আরো বাড়াতে চাই, যার জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম কলেজ সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাইকোলজি বিভাগের সাথে আলোচনা হয়েছে, একই সাথে অবৈতনিক প্রশিক্ষণের জন্য একটা কাঠামো তৈরি করা হয়েছে- যার বিস্তারিত নিয়ে মাননীয় পরিচালক স্যারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরেও কিছুটা আলাপ হয়েছে। সব দিক থেকে সম্মতি পেলে আমরা এই কার্যক্রম একটা নির্দিষ্ট কোর্স আকারে চালু করতে পারবো- যার ফলে একদিকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাইকোলজিস্ট তৈরী হবে, অন্যদিকে রোগীদের সরাসরি উপকার হবে।
মনের খবর: নিয়মিত ছোট ছোট কোর্স ও ওয়ার্কশপগুলোর কার্যক্রম শুরু করার পরিকল্পনা কবে থেকে বাস্তবে রূপ পেতে পারে?
ডা. পঞ্চানন আচার্য্য: আমাদের পরিকল্পনা আছে ছোট ছোট কিছু কোর্স বা ওয়ার্কশপ নিয়মিত পরিচালনা করা- যেমন সোশ্যাল স্কিল ট্রেনিং, স্ট্রেস কোপিং, ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স -এই ধরণের। যার মাধ্যমে প্রধানত এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হবে। এর বাইরেও আরো কিছু পরিকল্পনা আছে- যা সময়ে নির্ধারিত কাঠামোতে আনা হবে। তবে, আবারো বলছি- আমাদের ইচ্ছা অনেক, কিন্তু সাধ্য একেবারেই সীমিত। তাই তাড়াহুড়ো করে কোন কিছু শুরু করতে আগ্রহী নই, যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়ে বাস্তবসম্মত কিছু উদ্যোগ নিতে চাই ভবিষ্যতে – যাতে করে সেটা নিয়মিত চলমান থাকে।
মনের খবর: বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্যসেবাকে আরও কার্যকর করতে হলে সরকারের কোন কোন স্তরে পরিবর্তন বা পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি বলে আপনি মনে করেন?
ডা. পঞ্চানন আচার্য্য: এ বিষয়ে এতো কিছু বলার আছে যে, বিস্তারিত বলা এই মুহুর্তে সম্ভব নয়। তবে, সংক্ষেপে যদি বলি- বেশ কিছু স্তরেই পরিবর্তন আনতে হবে। যেমন- নীতিনির্ধারকদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়টিকে সত্যিকার অর্থেই গুরুত্ব দেয়ার মানসিকতা তৈরি, মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সকল খাতে বিশ্বমানের সাথে তাল মিলিয়ে অর্থবরাদ্দ দেয়া, বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিভিন্ন পদবীর পদ সৃজন এবং সেগুলোতে নির্দিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন জনবলকেই নিয়োগ দেয়া। কেন বললাম? কারণ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গবেষণা করে সুনির্দিষ্টভাবেই বলছে, মানসিক খাতে এক টাকা খরচ করলে পাঁচ টাকা লাভ পাওয়া যাবে। অন্যদিকে দেখুন, আমার মনোরোগবিদ্যা বিভাগে নতুন করে পাঁচটা পদ সৃজন হলো দীর্ঘদিনের সংগ্রামের পর। এখন তার মধ্য থেকে দুইটাতে অন্য বিভাগের লোকজন পদায়ন পেলো, যারা সাইকিয়াট্রি বিভাগের পদ ব্যবহার করে অন্য বিভাগে কাজ করবেন। এই মুহুর্তে হয়তো কেউ সাইকিয়াট্রিতে কাজ করার মতো নেই, তাই এটা আপাততঃ কোন সমস্যা না। কিন্তু ভবিষ্যতে আমার বিভাগে কেউ কাজ করতে আসতে চাইলে তখন কিন্তু এই দুইটা পদ আর পাবে না। এ ধরণের বিষয়গুলো আলাদাভাবে খেয়াল রাখা উচিৎ।
মনের খবর: মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে মেডিকেল শিক্ষার্থীদের মানসিক রোগ বিষয়ে সচেতনতা বা আগ্রহ বৃদ্ধিতে কোন উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে?
ডা. পঞ্চানন আচার্য্য: এ ব্যাপারে অনেক দিন ধরেই আলাপ আলোচনা হচ্ছে, অনেক কিছু উদ্যোগও নেয়া হয়েছে। তবে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাইকিয়াট্রি বিষয়টিকে যদি আরো উপভোগ্য ভাবে উপস্থাপন করা যায়, তাদেরকে সংযুক্ত করে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া যায়- যেমন কুইজ প্রতিযোগিতা; তবে, তাদের মধ্যে সচেতনতা বা আগ্রহ দুটোই বাড়বে।
মনের খবর: মানসিক রোগ প্রতিরোধ ও সচেতনতায় মিডিয়া, পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?
ডা. পঞ্চানন আচার্য্য: এতো একটা বিশাল মাপের আলোচনা। আপনি যেসব প্রতিষ্ঠানের কথা বললেন, সেসব প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু, প্রতিটা প্রতিষ্ঠান আমি বলবো বড়মাত্রায় ব্যর্থ। মূলধারার মিডিয়াতে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্পন্ন উপকরণ নেই মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে, মানসিক রোগ নিয়ে। সেখানে মনগড়া বিভিন্ন তত্ত্ব, তথ্য, ও ভুল কথা বার্তা দেদারসে প্রচারিত হয় বা ভুল ভাবে উপস্থাপন করা হয়। ফলে, সঠিক ধারণা গড়ে উঠার সম্ভাবনা ক্ষীনতর হতে থাকে। পরিবারের অধিকাংশই এ বিষয়ে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন, একইভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও। প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই মানসিক রোগকে অবজ্ঞা করা হয়, মানসিক সমস্যা আক্রান্ত কাউকে সহায়তার পরিবর্তে পদে পদে বাধা দেয়া হয়। এসবের পরিবর্তন দরকার।
মনের খবর: একজন চিকিৎসক ও শিক্ষক এই পরিচয়ে আপনি দীর্ঘদিন কাজ করছেন। নতুন প্রজন্মের মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় আগ্রহী চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে আপনার বার্তা কী হবে?
ডা. পঞ্চানন আচার্য্য: আমি শুরুতেই একটা কথা বলবো- স্বাস্থ্য বা চিকিৎসা শব্দের সাথে আমাদের জনমানস যে অর্থে সেবা শব্দটি যুক্ত করে সেই অর্থটা সঠিক নয়। স্বাস্থ্যসেবা বা চিকিৎসাসেবা বলতে এখানে মনে করা হয় এটি একটি Charity work- মানে এখানে একজন চিকিৎসক হাসিমুখে শুধু রোগীদের মন ভরিয়ে দেয়ার মতো কাজ করবেন, সবকিছু বিনামূল্যে হবে, তাঁর কোন চাওয়া-পাওয়া থাকবে না, অনেকটা এরকম যে- প্রভু-ভৃত্যের মতো একটা অবস্থান। আমি আবারো বলছি- সেবা শব্দটি আমাদের দেশে এভাবেই অর্থ করা হয়। কিন্তু এই সেবা শব্দটি আসলে Service- মানে একটা পেশা। তাই একজন চিকিৎসককে সাধু-সন্ত পর্যায়ের হতে হবে না, হতে হবে সর্বোচ্চ মানের পেশাজীবী। তাঁকে অর্জন করতে হবে পেশাগত দক্ষতা- যার একটা অংশ হচ্ছে মানবিক হওয়া, এটাই একমাত্র গুণ নয়। তাই, আমি নতুন প্রজন্মের মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় আগ্রহী চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই- একজন সর্বোচ্চ মানের সাইকিয়াট্রিস্ট হওয়ার দিকেই মনোযোগ দিতে, নিজের প্রফেশনালিজমকে আত্মস্থ করতে, এবং সেটার চর্চা করতে।
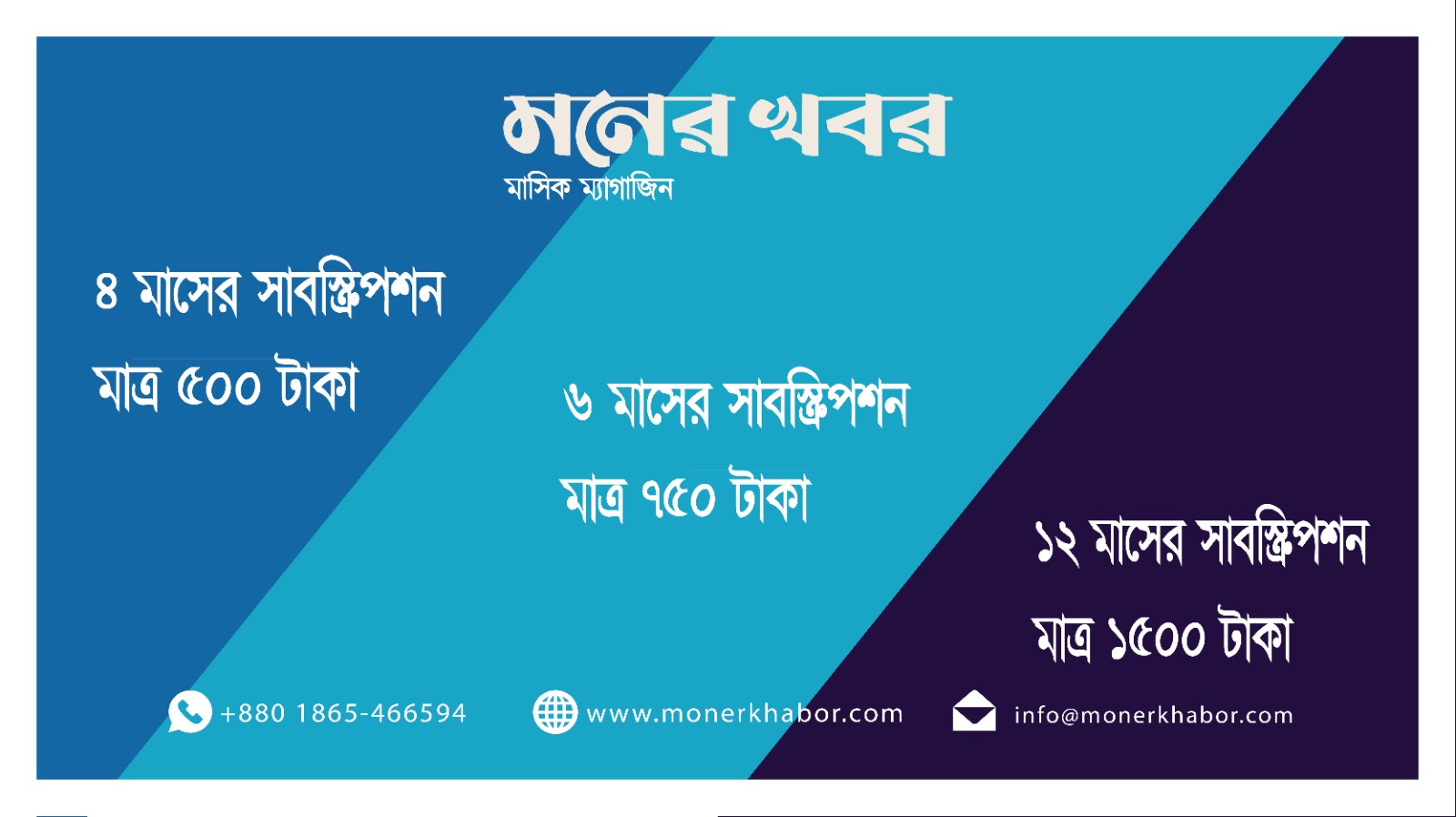
মনের খবর: মনের খবরের পাঠকদের উদ্দেশ্য মানসিক স্বাস্থ্য চিকিৎসা নিয়ে কিছু বলুন।
ডা. পঞ্চানন আচার্য্য: যদি একেবারেই সংক্ষেপে বলি- মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়টা নিয়ে সচেতন হোন, নিজের এবং অন্যের মানসিক স্বাস্থ্যে কোন সমস্যা হচ্ছে মনে হলে সহায়তা নিন- সাইকোলজিস্ট বা সাইকিয়াট্রিস্ট-এর। মনে রাখবেন, আপনি, আমি বা আমাদের কারোরই একটা কিছু মনে করা বা না করার উপর সত্যটা পালটে যায় না। সত্য যেটা- সেটা সত্যই থেকে যায়। মাঝখানে আমরা অবুঝের মতো নিজেদের কষ্টে ফেলি, যন্ত্রণায় ভুগি আর ধ্বংসের দুয়ারে উপনীত হই।
মনের খবর: মনের খবর এর কার্যক্রম কতোটা উপকারী এবং প্রয়োজনীয়।
ডা. পঞ্চানন আচার্য্য: মনের খবর-এর কার্যক্রমে আমি একেবারে শুরু থেকেই যুক্ত। আমি বলবো এটা আমার মনের প্রতিষ্ঠান- মনের ম্যাগাজিন। তবে, আমি নিরপেক্ষ ভাবেই অন্যদের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখেছি বারবার- কার কেমন লাগে? সবারই একই রকম প্রতিক্রিয়া- মনের খবর-এর বাঁধাই-প্রচ্ছদ-ডিজাইন-উপস্থাপনা অত্যন্ত উঁচুদরের; এর সব চেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে বিষয় নির্বাচন- এবং সেসব বিষয়ের উপর অনেক লেখকের মানসম্পন্ন সহজ ভাষার লেখা। সবার কাছে সেজন্য তথ্যগুলো হয় সহজবোধ্য, মনোগ্রাহী। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি- মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে সঠিক ধারণা গড়ে তুলতে মনের খবর অত্যন্ত উপকারী ও প্রয়োজনীয়।
“বাংলাদেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের মনোরোগবিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে আমরা ধারাবাহিকভাবে বিশেষ সাক্ষাৎকার নিচ্ছি। সেই ধারারই অংশ আজকের এই আলাপচারিতা।”
প্রকাশিত মতামত লেখকের একান্তই নিজস্ব। মনেরখবর-এর সম্পাদকীয় নীতি/মতের সঙ্গে লেখকের মতামতের অমিল থাকতেই পারে। তাই এখানে প্রকাশিত লেখার জন্য মনেরখবর কর্তৃপক্ষ লেখকের কলামের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে আইনগত বা অন্য কোনও ধরনের কোনও দায় নেবে না।
আরও দেখুন-