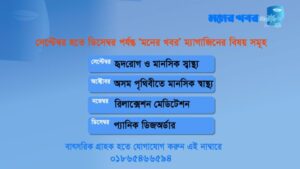(১২ মে, ১৮২০-১৩ আগস্ট, ১৯১০)
ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ১২ মে, ১৮২০ সালে ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মদিনকে সারা পৃথিবীতে ‘আন্তর্জাতিক নার্স দিবস’ হিসেবে পালন করা হয়। তিনি জাতিতে ব্রিটিশ ছিলেন। জন্মের সময় তাঁর পরিবার ইতালির ফ্লোরেন্সে অবস্থান করছিল, তাই ওই শহরের নাম অনুসারে নামকরণ করা হয়েছিল তাঁর। পিতা উইলিয়াম এডওয়ার্ড নাইটিঙ্গেল একজন প্রচন্ড বিদ্যানুরাগী মানুষ ছিলেন। ভিক্টোরিয়ান রক্ষণশীলতার যুগেও তিনি মেয়েদের গণিত, দর্শন, ক্ল্যাসিকাল সাহিত্য এবং বিভিন্ন ভাষা শেখার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। মা ফ্রান্সিস নাইটিঙ্গেল অভিজাত পরিবারের মানুষ ছিলেন।
ছোটোবেলা থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় পরিবারের সঙ্গে ঘোরার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। এরকম এক ভ্রমণের সময় প্যারিসে পরিচিত হয়েছিলেন ম্যারি এলিজাবেথ ক্লার্কের সঙ্গে। নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ম্যারি প্যারিসের বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। ম্যারি বিশ্বাস করতেন নারীরা পুরুষের সমকক্ষ। প্রকৃতপক্ষে তিনি ব্রিটিশ অভিজাত পরিবারের মেয়েদের এড়িয়ে চলতেন। ঘটনাক্রমে ফ্লোরেন্সের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল। এই বন্ধুত্বের সম্পর্ক টিকে ছিল প্রায় চল্লিশ বছর। ধারণা করা হয় ম্যারির ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ নাইটিঙ্গেলকে খুব বেশি অণুপ্রাণিত করেছিল।
এরপর নাইটিঙ্গেল গ্রিস ও মিশর ভ্রমণে যান। এথেন্সে অবস্থানকালে একটি ছোটো ঘটনা তাঁর মনকে খুব নাড়া দেয়। কিছু বাচ্চা দুষ্টুমির ছলে একটা ছোটো পেঁচাকে নিষ্ঠুরভাবে কষ্ট দিচ্ছিল। নাইটিঙ্গেল পাখিটিকে উদ্ধার করে তাঁর কাছে রেখে নাম দিয়েছিলেন এথেনা।
এরপর ১৮৩৭ সালে মিশরের থিবেসে ভ্রমণের সময় তাঁর অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়। মনে হতে থাকে সৃষ্টিকর্তা যেন তাকে ডাকছেন। তাঁর নিজের ভাষায় ‘God called me in the morning and asked me would I do good for Him alone without reputation.’ একজন অভিজাত পরিবারের মেয়ে কীভাবে এই সিদ্ধান্তে আসলেন তা নিয়ে আরো অনেক গল্প আছে।
ফ্লোরেন্সে জন্মালেও বেড়ে উঠেছিলেন লন্ডনের নিকটবর্তী ডার্বিশায়ারের গ্রামাঞ্চলে। ওই এলাকায় রজার নামে এক দরিদ্র রাখাল ভেড়ার পাল নিয়ে বসবাস করত। ভেড়ার পাল পাহারা দেয়ার জন্য ছিল পালিত কুকুর ক্যাপ। একদিন গ্রামের ডানপিটে ছেলের দল পাথর ছুঁড়লে ক্যাপের এক পা আঘাতপ্রাপ্ত হয়। রজারের পক্ষে একটি অকর্মণ্য আহত কুকুরকে পালার মতো আর্থিক সক্ষমতা ছিল না। সে কুকুরটিকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। অন্যদিকে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল কুকুরটিকে খুব ভালোবাসতেন। মাঝে মাঝে বাইরে বের হলে ক্যাপের সঙ্গে খেলতেন। সেদিন রাস্তায় বের হয়ে রজারের কাছে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন সব ঘটনা। মর্মাহত হয়ে স্থানীয় এক পাদ্রীকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাপকে দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন, ক্যাপের হাড় ভাঙেনি। স্রেফ জখম হয়েছে চামড়ায় কিছুটা। পাদ্রীর নির্দেশনায় গরম পানি, ব্যান্ডেজ দিয়ে তার শুশ্রূষা করলেন দুইদিন। এরপর কুকুরটি ভালো হয়ে যায়।
পরদিন রাতে ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৭ সালে স্বপ্ন দেখলেন অথবা এটা তার নিজস্ব অন্তর্দৃষ্টি ছিল যে, যেন তিনি ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করলেন তাঁর জীবনের বিশেষ লক্ষ্য রয়েছে। সৃষ্টিকর্তার তরফ থেকে এসবই তার জন্য ইশারা। হয়ত সেবা দিয়ে একজন মৃত্যু পথযাত্রীকে ফিরিয়ে আনা যায়, এই ঘটনায় এই বিশ্বাস তাঁর মনে গড়ে উঠেছিল।
১৮৪৪ সালে তিনি যখন প্রথম প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন নার্সিংকে পেশা হিসেবে নেবেন, পরিবারের তরফ থেকে তীব্র আপত্তি ছিল। বিশেষ করে তাঁর মা অভিজাত ব্রিটিশ হওয়ায় বিষয়টা মেনে নিতে পারছিলেন না। কিন্তু নাইটিঙ্গেল সেই সময়ের নারীদের মতো কারো স্ত্রী বা কারো মা হয়ে কাটাতে রাজি ছিলেন না। এটা সুস্পষ্ট বিদ্রোহ ছিল এবং তিনি প্রত্যয়ী ছিলেন। সোশ্যাল কগনিটিভ থিওরিতে ভাবলে বোঝা যায়, সেই সময়ের নারীদের জন্য রক্ষণশীল পরিবেশে তাঁর এই আচরণের কারণ ছিল তাঁর বাবার দেওয়া উন্মুক্ত জ্ঞান চর্চার পরিবেশ এবং বাবার সঙ্গে মেয়ের সম্পর্ক। কারণ পরিবেশ মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে, বদলাতেও পারে।
এরিকসনের সাইকোসোশ্যাল থিওরি মতে মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনে বড়ো নিয়ামক হলো তাঁর শৈশব, পিতা-মাতার ভূমিকা, আর সমাজ। এক্ষেত্রে ধারণা করা যেতে পারে নাইটিঙ্গেলের এই সিদ্ধান্তের পেছনে হয়ত ছিল সেই সময়ের সামাজিক রীতি-নীতি, নারীর প্রতি রক্ষণশীলতা ও উচ্চবিত্তের জীবনাচরণের প্রতি প্রতিবাদ।
এরপর ১৮৫০ সালে জার্মানিতে প্রটেস্টান্ট ধর্মযাজক থিওডর ফ্লেডনারের হাসপাতালে অসুস্থ ও বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর সেবামলূক কাজ দেখার সুযোগ পান। এই অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। তিনি সমস্ত সংশয় ঝেড়ে ফেলে মানুষের সেবায় জীবন উৎসর্গের ব্রত নিলেন। এখানেই চার মাস নার্সিং ও মেডিক্যাল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন যা তাঁর পরবর্তী জীবনের বুনিয়াদ হিসেবে কাজ করেছিল। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের সব থেকে বড়ো অবদান ছিল ক্রিমিয়ার যুদ্ধে আহতদের সেবায় আত্মনিয়োগ করা।
১৮৫৪ সালে সঙ্গে ১৮ জন নিয়ে স্বেচ্ছাসেবী তৎকালীন অটোমান সাম্রাজ্যের কৃষ্ণসাগরের নিকটবর্তী একটি অংশে কাজ করা শুরু করলেন। সেখানে তখন ভয়াবহ ঝুঁকিপূর্ণ স্বাস্থ্যব্যবস্থা বিরাজমান ছিল। যত রোগী যুদ্ধে আহত হয়ে মারা যাচ্ছিল তার চেয়ে দশ গুণ বেশি মারা যাচ্ছিল কলেরা, টাইফয়েড, টাইফাস এইসব রোগে। না ছিল পর্যাপ্ত ওষুধ, পরিচ্ছন্ন গজ ব্যান্ডেজ, সর্বোপরি ড্রেইনেজ বা সুয়ারেজের কোনো ব্যবস্থাপনাই ছিল না। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে কারো কোনো ধারণা ছিল না। আনুমানিক দুই হাজার সৈনিকের জন্য ছিল মাত্র চৌদ্দটি গোসলখানা। মানুষের শরীরে উকুন, চারপাশে মাছিদের বাজার। আবর্জনায় পরিপূর্ণ ছিল চারপাশ। নাইটিঙ্গেল এইসব দেখে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন সমস্যা মূলত তিনটি জায়গায়। খাবারে, আবর্জনা ও ড্রেইনেজ ব্যবস্থাপনায়। তিনি ব্রিটিশ সরকারকে অনুরোধ করে এইসবে আমূল পরিবর্তন আনেন। তিনি পরিচ্ছন্নতা ও মৃত্যুহারের মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে পেরেছিলেন। দিনরাত অবিশ্রান্ত খেটে গভীর রাতে মেডিক্যাল অফিসাররা চলে যাওয়ার পর হাতে আলো নিয়ে ঘুরতেন এক ওয়ার্ড থেকে আরেক ওয়ার্ডে। কোনো আহত সৈনিক কষ্ট পাচ্ছে কিনা নিজে গিয়ে শুনতেন। আর এই মানুষগুলো তাঁকে নাম দিয়েছিল ‘The Lady with the Lamp.’
ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ছিলেন একজন সুলেখিকা ও পরিসংখ্যানবিদ। ছোটোবেলা থেকেই প্রচন্ড ধর্মভীরু ছিলেন। এই যে জীবনব্যাপী কর্মযজ্ঞ নার্সিংকে আধুনিকীকরণ, সমাজ সংস্কার, পরিচ্ছন্নতার ধারণা পরিবর্তন, যাকে অনেকে বলেন নাইটিঙ্গেল পাওয়ার; এসব বুঝতে হলে তাঁর নিজস্ব বিশ্বাসকে বোঝা প্রয়োজন। তিনি আধ্যাত্মিক মানুষ ছিলেন। চিরাচরিত আধ্যাত্মিকতার মত মানুষকে সমাজ সংসার থেকে একদম দূরে নিয়ে আত্মমুক্তির কথা বলে। আবার কিছু মত আধ্যাত্মিকতায় উদ্বুদ্ধ মানুষকে প্রেরণা দেয় তাদের আত্মোপলব্ধি সমগ্র মানব জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দিতে।
ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল অনেক লেখা লিখেছেন আধ্যাত্মিকতার ওপর। লিখেছেন, ‘Where shall I find God? In myself’. অতিন্দ্রীয়বাদ, সুফিবাদের মতো শোনায় কথাগুলো। এই যে পরার্থপরতার উদাহরণ নাইটিঙ্গেল দেখিয়েছিলেন তার উদাহরণ আগে থেকেই খ্রিস্টান মিস্টিকদের মধ্যে ছিল। ক্যাথেরিন অব সিয়েনা, ক্যাথেরিন অব জেনোয়ার নাম বলা যায় উদাহরণ হিসেবে। এই সেবা করার তাড়না, মানুষের ভালোর জন্য কিছু করার আগ্রহ ও মানসিক শক্তির পেছনে হয়ত কাজ করে তাঁদের বিশ্বাস। হয়ত তাঁদের উপলব্ধি এমন যে এই শক্তি চলে আসে অলৌকিক উৎস থেকে, যার জন্য তাঁদের কোনো প্রচেষ্টার প্রয়োজন পড়ে না, স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসে। হয়ত এরকম বিশ্বাসই নাইটিঙ্গেলকে অনুপ্রাণিত করেছিল কিশোরীবেলা থেকেই।
তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য তাঁর বিশ্বাসকে মাদার তেরেসার মানব সেবার বিশ্বাসের সঙ্গে মেলানো যাবে না। মাদার তেরেসা ভাবতেন, ‘যন্ত্রণা, দুঃখ মানুষের প্রতি সৃষ্টিকর্তার সুন্দর দান, যাতে তারা যিশুর যন্ত্রণাকে বুঝতে পারে, সমব্যাথী হতে পারে’। কিন্তু নাইটিঙ্গেল ভাবতেন উপশমের কথা। ভাবতেন কীভাবে মানুষের যন্ত্রণা কমে, কীভাবে তার রোগ হচ্ছে, আর তা ঠেকানোর উপায় কী। তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিকতায় উদ্বুদ্ধ বিজ্ঞানমনস্ক সংস্কারক। তৎকালীন সময়ে নাইটিঙ্গেলের জন্য অনেকে অনুরক্ত থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র তাঁর মানব সেবা বাধাগ্রস্ত হতে পারে এই আশঙ্কায় আজীবন অবিবাহিতই ছিলেন। এই যে অদৃশ্য মানসিক শান্তি, তৃপ্তি যার জন্য অনেকেই বেছে নেয় এই জীবন, এই যে তাড়না তৈরি হয় মানুষের মনে অন্যের প্রতি সহমর্মিতা, করুণা ও ভালোবাসা দিয়ে সেবা দিয়ে যাওয়ার, তাকে আলবার্ট ফিনি ১৯৮২ সালে উল্লেখ করেছিলেন ‘ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল সিন্ড্রোম’ নামে। অনেকে আবার বলেন, ‘নাইটিঙ্গেল এফেক্ট’। তবে সুস্পষ্টভাবেই এটা কোনো রোমান্সের ওপর গড়ে ওঠে না। এই সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে মানুষের প্রতি মানুষের সহমর্মিতা, দয়াশীলতা এবং পেশাদার ইতিবাচক মনোভাব। এই সবগুলোই অসুস্থ মানুষের সেরে ওঠার জন্য খুব জরুরি। তবে এখানে পেশাদারিত্বের সীমারেখা থাকে। যার ভেতরে থেকে একজন মানুষ আরেকজন মানুষের দুঃখ দুর্দশা কমানোর জন্য সর্বোচ্চটা করতে পারেন।
ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল নিজে নার্সিং বিষয়ে পেশাদারিত্বের চরম উৎকর্ষতা দেখিয়েছিলেন। দায়িত্বের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত যত্নশীল। সার্বিক পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় তখনকার দিনের পুরুষদের সমকক্ষ ছিলেন। এই গুণ তাকে সবকিছু বদলাতে আর পরিবর্তন আনতে সাহায্য করেছিল। অনেকের মতে জনসাধারণ তাঁকে নিয়ে ভাবত, ‘Woman with a strong man’s character’. পরবর্তী জীবনের পুরোটা সময় নার্সিং পেশার উন্নয়নে, প্রশিক্ষণ প্রদানে পার করেছেন।
তিনি ১৮৬০ সালে প্রথম সেইন্ট থমাস হাসপাতালে নার্সিং স্কুল উদ্বোধন করেন। এছাড়া তিনি আমেরিকার প্রথম প্রশিক্ষিত নার্স লিন্ডা রিচার্ডস এর প্রশিক্ষক ছিলেন। ১৮৫৭ সালের পর থেকে মাঝেমাঝেই শয্যাশায়ী থাকতেন। অনেকে মনে করেন ব্রুসেলোসিস আর স্পন্ডাইলিটিসে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন তখন। ডিপ্রেশনও আসত মাঝে মাঝে। ১৩ আগস্ট, ১৯১০ সালে লন্ডনে ঘুমের মধ্যে শান্তিতে মৃত্যুবরণ করেন আজীবন মানুষের যন্ত্রণা লাঘবের জন্য কাজ করে আসা এই মহীয়সী নারী।
ডা. সৌবর্ণ রায় বাঁধন
সূত্রঃ মনের খবর মাসিক ম্যাগাজিন, ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যায় প্রকাশিত।
স্বজনহারাদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য পেতে দেখুন: কথা বলো কথা বলি
করোনা বিষয়ে সর্বশেষ তথ্য ও নির্দেশনা পেতে দেখুন: করোনা ইনফো
মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক মনের খবর এর ভিডিও দেখুন: সুস্থ থাকুন মনে প্রাণে